খাগড়াছড়ি জেলা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল অঞ্চল। এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সামাজিক কাঠামো এই অঞ্চলের জটিলতা নির্ধারণ করে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন, ভূমি অধিকার, এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত ও অস্থিরতা চলেছে। খাগড়াছড়ি কেবল একটি জেলা নয়; এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের অন্যতম প্রতিফলন। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের স্বায়ত্তশাসন, আঞ্চলিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং ভূমি ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, যদিও সেই চুক্তি নিয়ে ছিল অনেক বিতর্ক। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ গঠন করা হয়, ভূমি কমিশন তৈরি করা হয়, এবং সেনা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে এই চুক্তি নিয়ে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দেয়। ইউপিডিএফ এবং জেএসএস তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে এই আশায় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ধীরে ধীরে অনেক কমানো হয়। ইপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্টর হয়ে উঠে। তাদের ভূমিকা দ্বিমুখী—একদিকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দাবির প্রতিনিধিত্ব, অন্যদিকে সহিংস কার্যক্রমের মাধ্যমে অস্থিরতা বৃদ্ধি। ইপিডিএফ শান্তি চুক্তির অসম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সেনাবাহিনীর দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতিকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা মনে করে। তাদের লক্ষ্য হলো পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। খাগড়াছড়িতে ইপিডিএফ স্থানীয় রাজনীতি ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তারা ছাত্র ও যুব সংগঠন, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে প্রভাব বিস্তার করে। মাঝে মাঝে তাদের কার্যক্রম সহিংসতায় রূপ নেয়। স্থানীয় জনগণ তাদের প্রতি সমর্থন এবং সংশয়—উভয়ই অনুভব করে। সেনাবাহিনী বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা করেছে, ১৪৪ ধারা জারি করেছে এবং ইপিডিএফ ও জেএসএসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। নিরাপত্তার জন্য এসব পদক্ষেপ প্রয়োজন হলেও পাহাড়িরা মাঝে মাঝে তাদের পদক্ষেপকে ভয় প্রদর্শনের বলে মনে করে।
gnewsদৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন
ভারত এবং মিয়ানমার তাদের নিজস্ব পাহাড়ি অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা, কাচিন ও অন্যান্য জাতিগত গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের সংঘাত চলছে। সীমান্তের কাছে এবং ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্তগত সমস্যার কারণে আরও জটিল হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনী কেবল অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মোকাবেলা নয়, আঞ্চলিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাও করতে বাধ্য। ইপিডিএফের কার্যক্রমকে সেনাবাহিনী হুমকি হিসেবে দেখে, যা প্রায়ই সংঘর্ষের আকার নেয়।
ইপিডিএফের সশস্ত্র তৎপরতা বিগত আওয়ামী সরকারের শাসনকালে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। দেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বারবার আওয়ামী সরকারকে সতর্ক করেছে। ওই রিপোর্টগুলো সত্ত্বেও তৎকালীন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নীরব ছিল; সশস্ত্র গোষ্ঠীর কার্যক্রম রোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।
গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইউপিডিএফের বহুমুখী কৌশলগুলোতে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা যায়। পোস্ট-ইনসার্জেন্সি অপারেশনের সময় সেই বিভ্রান্তি আরো স্পষ্ট হয়—যাতে ইউপিডিএফ ও জেএসএসের রাজনীতিকে সামরিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক ছিল। প্রতিটি রিজিয়ন নিজের মতো করে সমস্যা ছোট করতে চেয়েছে; কিন্তু এসব স্বল্পমেয়াদি সমাধান কৌশলগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংকটের জন্ম দিয়েছে। তদুপরি নেতৃত্বের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে নীতিমালার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে নি—এই সুযোগেই ইউপিডিএফ ধীরে ধীরে উগ্রপন্থী রূপ ধারণ করেছে। অনেক সময় কোন কমান্ডার যদি নিজের উদ্যোগ নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, তাদের বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হতো বা পদোন্নতি বঞ্চিত করে অপারেশন ইউনিট থেকে প্রত্যাহার করা হতো।
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আরও কুশাসন নজিরও রয়েছে। নানিয়ার ‘টিআই’ (স্মারক) বা জনসদরের কাছাকাছি এলাকায় স্থানীয়ভাবে অনুমতি দিয়ে ইউপিডিএফকে অফিস চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল; যদিও ২০০৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন কাজীর হত্যার পর ওই সিটি বন্ধ করা হয়েছিল। ২০০৮ সালের নভেম্বরে রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর অফিস পুনরায় চালু করা হয়—তখন থেকে সংশয় আছে যে ওই কার্যালয় সংগঠনের রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে কি না। জরুরি অবস্থার পর সশস্ত্র আবাদ-বিচরণ কিছুটা কমলেও, রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠনিক কার্যক্রম বেড়েছে—বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ঘৃণা রাজনীতি ছড়িয়ে দেওয়া এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রদের প্রভাবিত করে নতুন ক্যাডার সংগ্রহে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।
সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ি অঞ্চল সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখোমুখি হয়েছে। ঘটনা শুরু হয় একটি ধর্ষণ অভিযোগ থেকে, যদিও মেডিকেল পরীক্ষায় শারীরিক আলামত পাওয়া যায়নি। একে কেন্দ্র করে সামাজিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং এটি এলাকায় অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনিশ্চিত এবং আঞ্চলিক প্রভাব ও সীমান্তগত সমস্যা আরও জটিলতা তৈরি করছে। নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ গুরুতর।
নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন, ইউপিডিএফের সন্ত্রাস বন্ধে এখনই কড়া ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি প্রমাণভিত্তিক তদন্ত, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা নিশ্চিত এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্য রক্ষার ব্যবস্থা।
বিশ্বের অন্যান্য দেশে পাহাড়ি জনগণও তাদের ভূমি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। মেক্সিকোর ওয়াক্সাকা অঞ্চলের পাহাড়ি জনগণ সরকারের অবহেলা ও ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে। এছাড়া, কলম্বিয়া সম্প্রতি আদিবাসী কাউন্সিলগুলিকে সরকারী স্থানীয় সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা তাদের স্বায়ত্তশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা প্রদান করেছে। এই উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে, আদিবাসী জনগণের ভূমি ও সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রাম একটি বৈশ্বিক সমস্যা।
বাংলাদেশের খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অস্থিতিশীলতা নিরসনে সেনা ক্যাম্প ও ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে অনেক মহলই পরামর্শ দিচ্ছে। বিশেষ করে খোদ খাগড়াছড়িতে কর্তব্যরত সেনাবাহিনী থেকে সেনা ক্যাম্প সংখ্যা ২৫০ টিতে উন্নিত করার পরামর্শ নিঃসন্দেহে বিবেচনার দাবি রাখে। যদিও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সেনা ক্যাম্প বাড়ানোর বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কিছু অংশের জনগণ মনে করেন যে, সেনা উপস্থিতি বাড়ানো তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। অন্যদিকে, কিছু জনগণ মনে করেন যে, অতিরিক্ত সেনা উপস্থিতি তাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং এটি তাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ রয়েছে কিনা সেটাও ভেবে দেখতে হবে।
সরকারের পক্ষ থেকে এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন অব্যহত রাখতে হবে। কৃষি, বনজসম্পদ, ক্ষুদ্র শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, নারী ও যুব সম্প্রদায়কে শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা এবং স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বিত সীমান্ত তত্ত্বাবধান ও সংঘর্ষ-নিরোধমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। মূল লক্ষ্য হলো তথ্যভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক নীতি গ্রহণ এবং পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ ও জীবনকে কেন্দ্রে রাখা। স্থায়ী সমাধানের জন্য সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করতে হবে যেন নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং জনগণের আস্থা পুনঃস্থাপিত হয়।
লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট


 ডেস্ক রিপোর্ট
ডেস্ক রিপোর্ট 










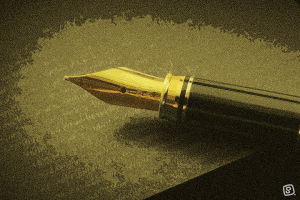



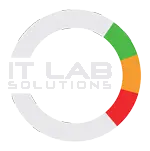 আইটি ল্যাব সলিউশন্স লি.
আইটি ল্যাব সলিউশন্স লি.